মজিবর রহমান
বয়স যখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই তখন ‘সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা’ নামক প্রথম গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে তাঁর। গ্রন্থাবদ্ধ ১২ প্রবন্ধের ১০টিই সমকাল, উত্তরাধিকার, গণসাহিত্যসহ তখনকার সুপরিচিত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত। লেখকের নিজের ভাষ্য থেকে জানতে পারি, গ্রন্থ প্রকাশকাল ১৯৮৫ পূর্ববর্তী ২০ বছর তিনি কিছু না কিছু লিখেই গেছেন। বস্তুতঃ সে কারণেই পাঠক পরিচিতির জন্যে তাঁকে গ্রন্থ প্রকাশঅবধি অপেক্ষায় থাকতে হয়নি, মননশীল লেখক হিসেবে খ্যাতি কুড়ান পূর্বেই। তিনি যতীন সরকার; লেখার সাহিত্য গুণ ও উপজীব্যর জন্যে যিনি কেবল বর্তমান নয়, ভবিষ্যতেও নিশ্চিত বিপুলভাবে পঠিত হবেন।
‘সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা’ প্রকাশিত হবার পর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ : ‘বাংলাদেশের কবিগান’, ‘বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য,’ ‘সংস্কৃতির সংগ্রাম’, ‘সংস্কৃতি ও বুদ্ধিজীবী সমাচার’, ‘মানব মন, মানব ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব’, ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন’, ‘পাকিস্তানের ভূতদর্শন’ প্রভৃিত। এছাড়া অহরহ প্রকাশিত হয়ে চলেছে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এ যাবত প্রকাশিত পুস্তকের ভেতর ‘পাকি¯তানের জন্মমৃত্যু দর্শন’’ বহুল সমাদৃত। গ্রন্থটি বাংলা দৈনিক ‘প্রথম আলো’ কর্তৃক মননশীল শাখায় পুরস্কৃত।
তিনি বিশ্বাস করেন বস্তুবাদ ও দ্বান্ধিক বস্তুবাদে; লেখালেখি ও ভাবনা চিন্তায় এর প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। ইতিহাস বিশ্লেষণে টেনে আনেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে। ইতিহাস যে কেবল রাজ-রাজড়াদের আগমণ-নির্গমন, উত্থান-পতনের কাহিনী নয়; এর উপজীব্য সমাজ ও সমাজের মানুষও— এ সত্য প্রকাশে তাঁর পটুত্ব লক্ষণীয় মাত্রার । যতীন সরকার আসলে বিশ্বাস করেন মার্কসবাদ-এ, যে-মার্কসবাদের ভিত্তি হলো এই বস্তুবাদ, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ । একে নির্ভর করে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ তাঁর অন্বিষ্ট, মার্কস-এর পাশাপাশি এঙ্গেলস ও লেলিনকে এর কারিগর মানেন। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উপর যতীন সরকারের যে-আস্থা সে-আস্থা সমাজতন্ত্র দুর্দশাগ্র¯ত হবার পরও বিস্ময়কর রকম অটুট। এ বিষয়ে পরে আমরা আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করবো।
দুই
যতীন সরকার নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়ায় যে-স্থানে জন্ম নিয়ে বাল্য ও শৈশব কাল কাটান সে-স্থানটিতে ছিলো হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত বসবাস। জন্মসূত্রে তিনি ধারণা পান জাতপাত নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধের, অবলোকন করেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক বিভেদের স্বরূপ। এছাড়া তেতািল্লশের মন্বন্তর,ছেচল্লিশের নির্বাচন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সাতচিল্লশ সালের দেশভাগ ও তার অগ্রপশ্চাৎ পরিস্থিতি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৬ সালে। ১৯৪৬-’৪৭ সালের ঘটনাপ্রবাহের সময় তাঁর বয়স মাত্র দশ কিংবা এগার। এতো অল্প বয়স-সময়কার ঘটনাবলী হৃদয়ে শক্ত আঁচড় কাটার কথা না, কিন্তু সেটি সম্ভবপর হয়েছিলো পারিবারিক আবহ, পারিপার্শ্বিকতা ও ব্যতিক্রমী মেধার কারণে।
১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগ উদ্ভূত পরিস্থিতিকে আমরা অনেকেই সরলীকরণ করে দেখি। ভাবি বুঝি সেটি সময়ের দাবি ছিলো; আর সেই দাবির সঙ্গে একাট্টা ছিলো সমগ্র জনগোষ্ঠী। প্রকৃতপক্ষে এ মনোভাব জাগ্রত ছিলো কেবল মুসলিম সম্প্রদায়ের ভেতর, হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের নিকট ছিলো সেটি এক কালো অধ্যায়। বিভাজন-পূর্ববর্তী দাঙ্গায় তারা যেমন ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো, তেমনি আতঙ্কের মধ্যে ছিলো বিভাজন-পরবর্তী সময়েও। সহায় সম্পদের মায়া ত্যাগ করে একদল দেশ ছাড়ে, অবশিষ্টরা থেকে গেলেও যন্ত্রণাবিদ্ধ হতে থাকে পদে পদে। তাদের সহায়-সম্বল-সম্পত্তির উপর শ্যেন দৃষ্টি পড়ে স্থানীয় প্রভাবশালীদের। ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেওয়াসহ নানান কূট-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে প্রভাবশালী এই গোষ্ঠীটি থেকে-যাওয়া অবশিষ্ট হিন্দুজনদের একাংশের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে, দেশান্তরী হতে থাকে তারা ধীরে ধীরে। প্রতিকূলতার ভেতরও যারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় তারা নিদেন পেক্ষে শহরে পাড়ি জমানোর কথা ভাবে, কেননা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রামের তুলনায় অেপক্ষাকৃত অনুকূল। পরিস্থিতি দৃষ্টে যতীন সরকারের মন বেদনায় নীল হতে থাকে ক্রমশ।
অবশ্য এর মধ্যে তিনি আশার আলোও দেখতে পান। মামার বাড়ি মুক্তাগাছায় বেড়াতে গিয়ে গাবতলীর হাটে গ্রাম্যকবি ইউনুছ আলী-র সুর করে পাঠ করা ‘পাকিস্তানের কবিতা’’ তাঁকে অভিভূত করে। কবিতার ক’টি চরণ তাঁর গ্রন্থ ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যূ দর্শন’ থেকে উদ্ধৃত হলো :
‘ঢাকায় রাজধানী হবে (২) উন্নতি হবে বাংলাদেশের ভাই।
হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশে থাকতে যেন পাই।
.....................................
দেখ ফজর আলী ঠাকুর দাসের এক উঠাইন্যা বাড়ি।’
বলা নিষ্প্রয়োজন যে কবি ইউনুছ আলীর এ কবিতা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় ঋদ্ধ। হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে শুধু এক দেশ নয়, এক উঠোন নিয়ে বসবাস করার পক্ষে আর্তি এই গ্রাম্য কবির। এ প্রসঙ্গে যতীন সরকারের মন্তব্য ; ‘তিনি ছিলেন একজন কৃষক কবি। আবহমান বাংলার কৃষকদের অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ঐতিহ্যই তিনি বহন করছিলেন। কৃষকের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা বা মৌলবাদের কোনো ঠাঁই কোনো দিনই ছিলো না। পাকিস্তান নামক একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র সৃষ্টিতে বাংলার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভূক্ত কৃষকদের অবদানই সবচেয়ে বেশি— এ কথা ঠিক। কিন্তু তারা সাম্প্রদায়িক চেতনাতাড়িত হয়ে পািকস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছেন— সেকথা ঠিক নয়। জমিদার-মহাজন চক্রের হাতে শোষিত নিষ্পেষিত হচ্ছিল যে কৃষক, সে কৃষকের সামনে পাকিস্তান আন্দোলন একটি অত্যন্ত মোহনীয় ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরেছিল। সে ছবিই মুসলমান কৃষককে পাকি¯তান আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিল। কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় নয়।’ (গ্রন্থ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৬)।
তিন
বলছিলাম যে, বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই অবস্থায় যতীন সরকার তাঁর প্রথম গ্রন্থ ‘সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা’ প্রকাশ করেন। এর আগের বিশ বছর তিনি নিয়মিতভাবে লিখে গেছেন যা প্রকাশিত হয়েছে সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকায়-ম্যাগাজিনে।। পরিবারের কল্যাণে অধ্যবসায় শুরু হয়েছিলো তাঁর বাল্যকালে। সে অধ্যবসায়ের স্বরূপ আমরা যারা তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি— জানি। সামান্যতম ফুরসতও তিনি নষ্ট করেননি পঠন-পাঠন ও লেখালেখি ব্যতিরেকে। কঠোর-অধ্যবসায় ও রূঢ় বাস্তবতার সমন্বয়ে গড়ে উঠে তাঁর সাহিত্যমানস। সে-সাহিত্য শুধু ‘শিল্পের জন্যে শিল্প’-মুখীন নয়, বরং শৈল্পিক আবরণে জীবনের গল্প গাথায় সমৃদ্ধ এক উচ্চ মার্গের সাহিত্য সেটি।
শুধুমাত্র বয়স ৩০ পেরিয়েছে কেবল, এরই মধ্যে ১৯৬৭ সালে, বাংলা একাডেমির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর দীর্ঘ ও মূল্যবান এক প্রবন্ধ। শিরোনাম ‘পাকিস্তানোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা’। প্রবন্ধটির জন্যে ‘ডক্টর এনামুল হক সাহিত্য পদক’ প্রাপ্ত হন তিনি। খুব কষ্টসাধ্য উপস্থাপন ছিলো সেটি। ১৯৪৭ সাল হতে প্রবন্ধ রচনাকাল ১৯৬৭ পর্যন্ত প্রকাশিত পূর্ব বাংলা-পূবর্ পাকিস্তানের সমুদয় উপন্যাস নিয়ে আলোচনা চাট্টিখানি কথা নয়। আলোচনার সূচনা পর্বে মুসলিম ঔপন্যাসিকের সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ নিয়ে বলতে গিয়ে নজিবর রহমানের ‘আনোয়ারা’ ও কাজী ইমদাদুল হকের ‘আবদুল্লাহ’র প্রসঙ্গ টেনেছেন। নজিবর রহমান এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ এবং তাঁর ‘আনোয়ারা’ বহুল পঠিত হলেও, বেশি স্বার্থক আসলে ‘আবদুল্লাাহ’র রচয়িতা কাজী ইমদাদুল হক। যতীন সরকারের মূল্যায়ন : “নজিবর রহমান-এর পর সত্যিকারের স্বার্থক উপন্যাস রচিত হয় কাজী ইমদাদুল হকের হাতে । সমাজ-বীক্ষণের বিচারে তাঁর আবদুল্লাহ-র তুলনা চলে শরৎচন্দ্রের ‘পল্লী সমাজ’-এর সঙ্গে। এ উপন্যাসে মুসলিম সমাজের অন্ধ পীরভক্তি,গুরুপূজা, ধর্মের নামে সংস্কারপ্রিয়তা, পর্দা প্রথা, আশরাফ-আতরাফ সমস্যা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে পরিশীলিত মননশীল দৃষ্টিতে। নবযুগের যথার্থ ঔপন্যাসিকের মননশীল ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন কাজী ইমদাদুল হক; নজিবর রহমানের সে দৃষ্টির অভাব ছিলো।”
এই সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি ও সমাজবীক্ষণের আজন্ম পূজারী যতীন সরকার। ১৯৪৭ হতে ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ হতে ১৯৬৭-এর প্রথম ভাগ; অর্থাৎ দেশ বিভাগ-পরবর্তী কুড়ি বছরে প্রকাশিত উপন্যাস সমূহের পাতায় পাতায় খুঁজে বেরিয়েছেন তিনি সমাজ মনস্কতার ছাপ; সেই সঙ্গে অনুসন্ধান করেছেন বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী প্রগতিমুখীন উপাদান, এবং পক্ষে থেকেছেন ওই ধারার; তবে শিল্পগুণকে বিসর্জন দিয়ে নয়। ঘাম জড়ানো এই কাজের সম্পন্ন বক্তব্য : ‘আমাদের উপন্যাস শিল্পে বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগত ও গুণগত উত্তরণও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতেই প্রাথমিক দুর্বলতা কাটিয়ে আমাদের উপন্যাস সাহিত্য সমৃদ্ধতর হয়ে উঠবে— এমন আশা পোষণ করার পশ্চাতে যথেষ্ট হেতু বর্তমান।’ তাঁর এ আশাবাদের নিপূণ বাস্তবায়ন এখন দৃশ্যমান। একটা সময় ছিলো যখন পশ্চিমবঙ্গের উপন্যাস ছাড়া আমাদের তৃষ্ণা মিটতো না। এখন আর সে-অবস্থা নেই, বাংলাদেশের উপন্যাসজগত আলো ছড়াতে শুরু করেছে। সত্যরূপ পাচ্ছে যতীন সরকারের আশাবাদ।
যতীন সরকারের অন্বিষ্ট সম্পর্কে ইতোপূর্বে আভাস দিয়েছি, বলেছি তাঁর সাহিত্য কর্মের নিটোল শিল্পগুণ নিয়েও। সাবলীল ও ছান্দসিক গদ্য তাঁর, বিষয়বস্তু অন্বিষ্টের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। অসংখ্য উদ্ধৃতি, বিপুল তথ্য উপাত্ত ও তথ্যসূত্রে ঠাঁসা একেকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ-গ্রন্থ। উদ্ধৃতির ব্যাপক ব্যবহার প্রতিবন্ধক হয়নি কোথাও গদ্যগতির। সে কারণে জটিল বিষয়বস্তু আর জটিল থাকে না। অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার ব্যাপক মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও পড়ে ফেলা যায় একেকটি ‘লেখা’ টানা মনোযোগ সহকারে। প্রকাশের এই সাবলীলতার মূল কারণ জ্ঞানের ব্যাপ্তি। কঠিন কথা সহজ করে বলা যায় তখনই যখন ‘বিদ্যার দৌড়’ থাকে দিগন্তজোড়া। যতীন সরকার এসব ক্ষেত্রে অনন্য, তাঁর জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ, অভিজ্ঞতা প্রখর।
যতীন সরকারের কাম্যতার চূড়া সম্পর্কে একটি ধারণা আমরা পেয়েছি। চূড়ায় আরোহণের যজ্ঞনিনাদসরূপ তিনি ইতিহাসব্যাখ্যায় সামাজিক মন¯তত্ত্বের প্রয়োগ চান, আকুতি প্রকাশ করেন সমাজতন্ত্রমুখীন বৈষম্যবিরোধী অসাম্প্রদায়িক সমাজের জন্যে, যার উপাদান খুঁজে বেড়ান তিনি বাঙালির লৌকিক ঐতিহ্যে, শিষ্ট সাহিত্যসহ শিল্পকলার সকল ¯তরে।
চার
ইতিহাস ব্যাখ্যায় সামাজিক মন¯তত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়ে একটু ইঙ্গিত ইতোপূর্বে দিয়েছি। এ ব্যাপারে তাঁর সমর্থন জোরালো । গুরুত্বপূর্ণ এ অনুসঙ্গটি নিয়ে পুনঃপুন ভাবনা চিšতা যতীন সরকারের মতো অন্য কেউ করেন কিনা সন্দেহ আছে । সম্ভবত তিনি এ জাতীয় ভাবনার অগ্রপথিক আমাদের দেশে । সত্যিইতো অন্তরঙ্গকে না জেনে বহিরঙ্গের ইতিহাস রচিত হয় কী করে?
সমাজের প্রবণতা-প্রথা-ভাবাবেগ ও মানস গঠন, বিভিন্ন যুগে মানুষের মনের প্রকৃতি-মানসিক পরিবর্তনের ধারা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মানসগঠনের বিভিন্নতা প্রভৃতি সামাজিক মন¯তত্ত্বের উপাদান; যা ইতিহাসের উপকরণ। রুশ বিপলবের মহানায়ক ভ্লাাদিমির ইলিচ লেনিন বিপ্লবের প্রয়োজনে এই মন¯তত্ব অনুধাবনের প্রয়াস নিয়েছিলেন। যতীন সরকার অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন পাকি¯তান আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাজ-মনস্তাত্বিক পটভূমি। তিনি এ ক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়েছেন সাহিত্যের, সাহিত্যকে এর প্রধান উৎস ভাবেন। যদিও ললিতকলার অন্যান্য শাখা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তাঁর কাছে। সাহিত্যের মতো কোন বিশেষ যুগের সঙ্গীত ও চিত্রকলা সে-যুগের মানুষের অšতঃপ্রবণতা ও আশা আকাক্সখার প্রতীক।
‘ইতিহাস ব্যাখ্যায় সামাজিক মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য’ যতীন সরকারের খুব জ্ঞানগর্ভ একটি প্রবন্ধ। আবুল মনসুর আহমদের ‘জীবন ক্ষুধা ’ ও শহীদুল্লা কায়সারের ‘সংসপ্তক’ উপন্যাস দুটির সহায়তা নিয়ে তিনি ইতিহাস ব্যাখ্যায় সামাজিক মন¯তত্ত্ব প্রয়োগের বিষয়টি খোলাসা করেছেন। এর সারসংেক্ষপ অনেকটা এরকম :
দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশের ভূভাগ ছিলো পুরোদস্তুর কৃষিপ্রধান, সেই সূত্রে প্রায় সর্বাংশের জীবিকা ছিলো কৃষি। অর্থাৎ এর আধিবাসীদের গরিষ্ঠ অংশ ছিলো কৃষক, আবার এই কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলো মুসলমান। কৃষি প্রধান এই ভূ-খন্ডে কৃষকদের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোন আন্দোলনই সফল হওয়ার কথা ছিলো না। কৃষক সমাজ সেটি হতে দেয়ওনি; তারা, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক, পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেয়। কিন্তু সবাই-যে দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে পাকি¯তান প্রতিষ্ঠার দাবি সমর্থন করেছিলো এমন নয়। কৃষক সমাজের অধিকাংশই তখন ছিলো হতদরিদ্র বা ভূমিহীন। এরা ভেবেছিলো পাকি¯তান প্রতিষ্ঠা হলে জমির মালিক হওয়া যাবে, কিংবা তাদের দৈন্যদশা ঘুচবে। একই সঙ্গে সম্পন্ন মুসলমান কৃষকদের স্বপ্ন ছিলো ভিন্নরকম। তারা হিন্দু জমিদার জোতদারদের স্থলাভিষিক্ত হতে চাইলো। তখনকার দিনে জমিদার, জোতদারদের অধিকাংশ ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।, মুসলমানরা ছিলো এখানে সংখ্যায় অতি নগণ্য। তারা প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছিলো না। পাকি¯তান নামক স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলে সেই প্রতিযোগিতা আর থাকবে না, উপরন্তু হিন্দু জমিদার-জোতদাররা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে; আর তখন সেসবের মালিক হবে সম্পন্ন মুসলমান কৃষকরা— এটি ছিলো পাকি¯তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হবার প্রেরণা তাদের। অপরদিকে হিন্দু সম্প্রদায় স্বভাবতই এই দেশ বিভাগের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলো, ছিলো উৎকণ্ঠিত নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে। এই-ই ছিলো মন¯তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ যা ইতিহাস ব্যাখ্যায় খুব সামান্যই মনোযোগ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, সম্পন্নরা হতদরিদ্রদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ নানা স্বার্থসিদ্ধির কাজে কেবল ব্যবহারই করেছে, স্বার্থ হাসিলের পর তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। আসলে প্রগতিমুখীন সমাজ বিপ্লব ছাড়া দরিদ্রের ভাগ্য ফেরানো সম্ভবও না।
বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিয়ে রচিত ইতিহাসেও সামাজিক মন¯তত্ত্বের প্রয়োগ চোখে পড়ার মতো নয়। তখনও বাংলাদেশ গ্রাম ও কৃষি প্রধান; মোট জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ কৃষিজীবী বা কৃষক। তবে পরিবর্তন একটা ঘটে গিয়েছিলো, সেটি মধ্যবিত্তের বিকাশ; যার ইঙ্গিত যতীন সরকার দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। এই মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী মূলত কৃষকের সšতান। ফলে কৃষকের স্বার্থ, আর মধ্যবিত্তের স্বার্থ একাকার হয়ে যায়। পাকিস্তান শাসনামলে কৃষকদের শ্রীহীন অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। উৎপাদনের উপকরণ প্রাপ্তি, কিংবা পুঁজি সরবরাহসহ কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা তারা পায়নি। নব উত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ছিলো বঞ্চনার শিকার। শাসকগোষ্ঠীর পক্ষপাতিত্ব ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর দিকে। মোট জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশের বাস পূর্ব পাকি¯তানে হলেও শিল্প ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই গড়ে উঠে পশ্চিম পাকি¯তানে; পূর্ব পাকি¯তান ছিটেফোটার ভাগ পায়। এমনকি ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ছিলো অবজ্ঞার মনোভাব। এসব কারণে জনমন¯তত্ত্ব ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে। বাস্তবতা প্রতিফলিত হচ্ছিলো বাংলার কবিতায়, গানে, সিনেমায় যার যৎকিঞ্চিত উেল্লখ যতীন সরকারের লেখায় পাওয়া যায়। নিজে বেশি ব্যাখ্যায় না গিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ইতিহাস প্রণেতাদের।
তবে তাঁর ইতিহাস আশ্রিত লেখায় সামাজিক মনস্তত্বের প্রয়োগ ব্যাপক। ‘পাকি¯তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন’ ও ‘পাকিস্তানের ভূতদর্শন’ এর উজ্জ্বল দৃষ্টাšত। গ্রন্থ দুটিতে নিজের জীবন ও জীবনদর্শন- নির্ভর কথার পাশাপাশি উঠে এসেছে ইতিহাস। সে ইতিহাসকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন সামািজক মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর। ব্যাখ্যা-বিশেলষণের বেলায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আশ্রয় ত্যাগ করেননি।
ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও মনে করি ইতিহাস ব্যাখ্যায় সামাজিক মন¯তত্ত্বের প্রয়োগ অধিক মাত্রায় হওয়া উচিত। সাহিত্যসহ শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম ও পুরাকীর্তিতে জনমনস্তত্ত্ব দীপ্যমান; কাজে লাগাতে পারলে ইতিহাস ঋদ্ধ হবে।
পাঁচ
ইতিহাস ব্যাখ্যায় সামাজিক মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ তত্ত্বের মতো আরেক তত্ত্ব হলো লেনিন সমর্থিত ‘সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ’। যতীন সরকার সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের এ দর্শনকে মানেন। ‘সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা’ নামক গ্রন্থে গ্রন্থিত প্রবন্ধ ‘সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ : উদারতা-অনুদারতার দিগন্ত রেখা’-তে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন এভাবে : “শিল্পের স্রষ্টা মানুষ; মানুষের সমস্ত কৃতি উতসারণের মূলে আছে সমাজবদ্ধতা; সমাজ বিকাশের নিয়মকে অস্বীকার করে মানুষের সকল কৃতির মতোই শিল্পকৃতিও সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। আবার সমাজ বিকাশের একটি অপরিহার্য পর্যায় রূপেই উদ্ভব সমাজতন্ত্রের, সমাজতন্ত্রই এ পর্যায়ে অমোঘ বা¯তব। সেই বাস্তবের অমোঘ নিয়ম প্রণালীকে অস্বীকার করার উপায় নেই শিল্প সাহিত্যের পেক্ষও। এ পর্যায়ের এই বাস্তবতার নামই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ । এ-বাস্তবতা বাস্তবের প্রকাশকে কালের প্রেক্ষাপটে রেখে বিচার করে বলেই বাস্তবের অতীত আর বর্তমানকেই শুধু দেখে না, দেখে ভবিষ্যতকেও, —যা আছে বা ছিল শুধু তাকে নয়, যা হবে বা হতে পারে তাকেও। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বা¯তবতার কালগত মাত্রা তিনটি— অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। আর দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যেহেতু নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পেরেছে যে, বস্তুর গতি নানা চড়াই উতরাই বেয়েও ক্রমাগত নব নব বিকাশের অভিমুখী, সেহেতু সমাজতান্ত্রিক বা¯তববাদও সমাজের তথা মানুষের ভবিষ্যৎ প্রগতি সম্পর্কে নিঃসংশয়। তাই এ বা¯তববাদের অনুসারী যে শিল্পী বা সাহিত্যিক, তিনি কখনও নৈরাশ্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী, অনিশ্চয়তাবাদী হতে পারেন না।”
এর আগে তিনি সাহিত্য েক্ষত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন ‘বাদ’ যেমন— ভবিষ্যৎবাদ, প্রকাশবাদ, ডাডাবাদ,পরাবাস্তব্বাদ, অ¯িতত্ববাদ প্রভৃতি বাদের উপর নিজের অনাস্থার কথা জানান। পাশাপাশি স্মরণ করিয়ে দেন : “শিল্পে বা¯তবতার প্রকাশ ঘটানো মানে বা¯তবের অনুলিপি বা অনুকরণ নয়, এটি হচ্ছে এমন একটি বিশিষ্ট নান্দনিক যথার্থতা যা আসলে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করবার,উপলব্ধি করবার ও পরিবর্তন করবার হাতিয়ার বিশেষ। ” আরেকটি উদ্ধৃতি— “সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প যা মানুষের নিকট নতুন কিছুর অভিব্যক্তি ঘটায়, যা তার মন-মানস, আবেগ ও আকাক্সখার সমৃদ্ধি সাধন করে, যা প্রত্যেকের ভিতরকার শিল্পী সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। ” (সূত্র : পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) ।
যতীন সরকারের বিচার বিেশ্লষণ দ্বান্দ্বিক প্রকৃতির। মন্দ দিকটাও তাঁর চোখ এড়ায়নি। তাঁর নিজের জবানী : “... বস্তুর বিকাশ—যে নির্দ্বান্ধিক নয় এ-তো বস্তুবাদেরই আবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত। তাই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদও স্বাভাবিক ধারায় স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর মতো দ্বন্দ্বহীনভাবে বিকশিত হতে পারেনি। বহু সংকীর্ণতার শৈবালে তা আচ্ছন্ন হয়েছে, অনুদারতার চূড়ায় ঠেকে গেছে বহুবার। শিল্পে সাহিত্যে বাস্তববাদ যখন ‘সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ’ নাম পরিগ্রহ করেনি, তখনও তাকে বিশুদ্ধ সমাজতান্ত্রিক ছকে বেঁধে ফেলার প্রয়াস দেখা গেছে। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরপরই সোভিয়েত ইউনিয়নের একদল অতি উৎসাহী সমাজতন্ত্রী সাহিত্য-সংস্কৃতিকে একটা সংকীর্ণ ধারায় প্রবাহিত করার উদ্যোগ নেয়। সর্বহারার এক অভিনব সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টির নামে ‘প্রোলেটকাল্ট’ নামে একটা গোষ্ঠী কোমর বাঁধে প্রাক-সমাজতন্ত্রী যুগের সব শিল্প-সংস্কৃতিকে উৎসাদনের লেক্ষ।
শিল্প সংস্কৃতির কমল বনে এই মত্ত হ¯তঁীর মত্ততাকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেন স্বয়ং লেনিন। বাস্তবের ইতিহাসকে অস্বীকার করে বাস্তবের ব্যাখ্যা অচল; অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ—বাস্তবের এই তিন মাত্রাকেই যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার নাম বাস্তববাদ —এই সত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করার জন্যই লেনিন জানিয়ে দেন : ‘মার্কসবাদ যে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ হিসেবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে তার কারণ এই মতবাদ বুর্জোয়া আমলের সব থেকে মূল্যবান উপাদানগুলোকে বর্জন না করে বরং তাদের আত্মস্থ করেছে এবং দু’হাজারের বেশী বছরের মানব সভ্যতা ও চিন্তার যা কিছু মহৎ তাকে নতুন আকারে গড়ে তুলতে পেরেছে।’
লেনিন নির্দেশিত এই সত্য সংকীর্ণতা আর অনুদারতার বিরুদ্ধে এক অমোঘ রক্ষাকবচ। এই সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন বলেই লেনিন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ নান্দীকার মায়াকোভস্কির চেয়ে ‘বুর্জোয়া’ পুশকিনের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন, আর তলস্তয়কে বাঁচাতে পেরেছিলেন উৎসাহের আতিশয্যে টগ্বগ্ করা তরলমতি ‘কমিউনিস্ট’-দের অন্যায় আক্রমণের হাত থেকে। তল¯তয়ের কৃতির মূল্যায়ণ করতে গিয়েই লেনিনের হাত দিয়ে বেরিয়ে আসে বিপ্লবী শিল্পী সাহিত্যিক সম্পর্কে সেই বিখ্যাত অনুসিদ্ধান্ত : ‘কোনো শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ হন, তবে তাঁর রচনায় িবপ্লবের কোনো না কোনো মর্মগত অংশ প্রতিফলিত না হয়ে পারে না।’ (সূত্র : প্রবন্ধ : সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ : উদারতা-অনুদারতার দিগন্তরেখা)। তল¯তয়কে এমনকি রুশ বিপ্লবের দর্পণ বলে উল্লেখ করেছিলেন লেনিন।
যতীন সরকার লেনিন সমর্থিত সমাজতান্ত্রিক বা¯তববাদের অনুসারী। অতীতের সুকীর্তিকে বর্জন করে নয়, বরং তাকে পাথেয় করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে প্রত্যয়ী। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ ‘বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য’ এই দর্শনের দলিল।
যতীন সরকার অতঃপর সেই ঐতিহ্য সন্ধানে ব্রতী হন। তাঁর অনুসন্ধান শেকড় খুঁজে পায় যেমন শিষ্টজনের মতামত ও শিষ্ট সাহিত্যে, তেমনি সংিশ্লষ্টতা পায় লোক সাহিত্য ও লৌকিক ঐতিহ্যে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উপদানসমূহ বস্তুত সমাজতন্ত্রের ছায়াপাত বা এর অন্তঃসার। কোনটি ‘সমাজতন্ত্র’ নামক অভীপ্সা উদ্ভাবনের পূর্বের, কোনটি পরের। উপাদানসমূহ পরিস্ফুট কখনো অসাম্প্রদায়িকতার প্রকাশে ও সাম্য চিšতায়, কখনোবা কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞানমনষ্কতায়, মুক্ত চিন্তায়; কিংবা প্রগতি চেতনায়। যতীন সরকার এ পর্যায়ে বেছে নিয়েছেন রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলসহ খ্যাতনামা শিল্পী সাহিত্যিকের সৃজনকর্ম, দৃষ্টি নিেক্ষপ করেছেন লৌকিক ঐতিহ্য ও লোক মানসে, হাতড়ে বেড়িয়েছেন বেদ-বেদান্ত -পুরাণ।
ছয়
যতীন সরকার কলেজ জীবন থেকে সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে আবিষ্ট রাজনীতিক ও প্রগতিমুখীন ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে আসেন। ধীরে ধীরে নিজেও সে-ভাবাদর্শে আত্মলীন হয়ে যান, এবং এক পর্যায়ে সক্রিয় হয়ে উঠেন সাম্যবাদী রাজনীতিতে। এই সক্রিয়তা যতোটা না নেতাকর্মী রূপে, তার চাইতে বেশি তাত্ত্বিক পরিচয়ে। মার্কসবাদী পন্ডিত হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। অন্য দশ জনের মতো তিনি কেবল ‘অনুসারী’ নন, সর্বদাই সৃজনশীল ও চিন্তক। বস্তুবাদ-দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মার্কসবাদের ভিত্তি। এই প্রত্যয়গুলি তিনি আত্মস্থ করেছেন নিবিড় মনোযোগ সহযোগে; লেখালেখিতে তার প্রয়োগও করেছেন সিদ্ধহ¯েত। তাঁর ব্যক্তি মানসের সহিত মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনবাদ সর্বদাই একাকার।
পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মতো ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পীঠস্থান সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পতনের পরের বছর ১৯৯২ সালে, ‘মার্কসবাদের খন্ডীভবন ও সমাজতন্ত্রের সংকট’ শীর্ষক যে প্রবন্ধটি তিনি রচনা ও প্রকাশ করেন তা আত্মসমালোচনার এক অনুপম আখ্যান। ওতে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে দুটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেন। বিষয় দুটি হলো মার্কসের ‘বিচ্ছিন্নতা বিষয়ক তত্ত্ব’ ও ‘রাষ্ট্র বিলোপ মতবাদ’ —যা সোভিয়েত নেতৃত্ব আমলে নেননি। এছাড়া ‘শ্রমিক শ্রেণীর এক নায়কত্ব’ ও ‘গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা’ নিয়েও কথা বলেন তিনি।
ধনতন্ত্রী সমাজ থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পূর্বে ‘শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব’-ধর্মী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকবে বলে মার্কস মত ব্যক্ত করেছিলেন। লেনিন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ‘গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা’র নীতি। যতীন সরকারের লেখা থেকে আমরা জানতে পারছি— এ দু’য়ের কোনটিরই সঠিক বা¯তবায়ন হয়নি। ‘শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব’ রূপ নেয় পার্টি একনায়কত্বে। লেনিনের ‘গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা’ তত্ত্বে সংগঠনের সকলের জন্যে গণতন্ত্র চর্চার ব্যবস্থা ছিলো, অপব্যাখ্যা-অপপ্রয়োগের কারণে সেই তত্ত্ব পরিণত হয় ‘হৃদয়হীন কেন্দ্রিকতা’-য়।
সব মিলিয়ে সারকথা দাঁড়ায় : লেনিন-উত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসন প্রণালী পার্টির একনায়কত্ব ও সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র দ্বারা চরম মাত্রায় দূষিত হয়ে পড়েছিলো। পরিণতিতে শাসক শ্রেণী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতা ও আলোচিত-অনালোচিত বিবিধ উপসর্গ ধ্বসের কারণ হয়ে সমাজতন্ত্র নামক ন্যায়ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটায়; সেটি কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নে নয়, গোটা বিশ্বে।
বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন মানে একটি আদর্শের পতন, ধনতন্ত্র নামক বৈষম্যযুক্ত সমাজের বিপরীতে ন্যায়ভিত্তিক বিকল্প সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্নে গুড়েবালি। এই স্বপ্নসাধ পূরণের আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি সরে দাঁড়াননি মোটেও, ভুল ত্রুটি শুধরে সামনে এগোনোর পক্ষে অবস্থান তাঁর। ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি আয়োজিত রুশ বিপ্লবের শত বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে পঠিত ‘অক্টোবর িবপ্লব ফিরে দেখা ও সামনে তাকানো’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধে একই রকম অভিমতের প্রকাশ দেখি তাঁর। সমাজতন্ত্রকে অন্বিষ্ট করার প্রত্যয়ে দীপ্ত সর্বদাই। সত্যিই তিনি বিশ্বাসে অটল এক মহীরুহ ।
প্রাবন্ধিক,কলাম লেখক



.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)



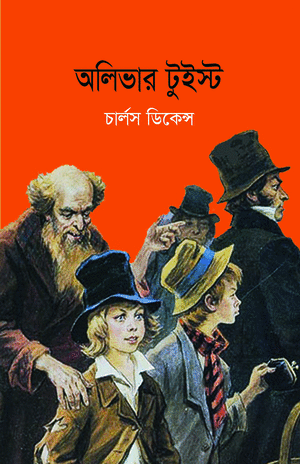


.jpeg)



0 মন্তব্যসমূহ