‘বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক’ গ্রন্থটি পড়ে আমার মনে হয়েছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট বিশ্বসাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক সম্পর্কে গ্রন্থকার যে বিশ্বস্ত রূপরেখা মুন্সিয়ানার সাথে উপস্থাপন করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। মনে পড়ে, প্রবীণ সমুদ্রচারী ইউলিসিস সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে অমিত সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশির মতো জ্ঞানরাজ্যের দুর্দমনীয় হাতছানির প্রতি অঙুলি নির্দেশ করছেন।
সাহিত্যের সবচেয়ে বিচিত্র ও শক্তিশালী শাখাসমূহের অন্যতম হচ্ছে উপন্যাস, যার বৈচিত্রময় বর্ণনার মাধ্যমে মানবজীবনের জটিল অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত প্রতিফলিত হয়। গল্প বলার ঢঙে শুরু হলেও উপন্যাস বর্তমানে বিশ্বসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভরূপে একই সাথে চলমান সমাজের দর্পণ ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। কালের বিবর্তন, ভৌগোলিক পরিবর্তন কিম্বা বিষয়বস্তুর অনন্যতা কোনোকিছুই উপন্যাসের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সবকিছুই চিত্তাকর্ষক করে তোলা যায়। আর তা হয়ে থাকে ঔপন্যাসিকের কারিশমায়। জীবন ও জগৎ সম্পর্ক তাঁর ধারণা, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি উপন্যাসকে শিল্পম-িত করে। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত, তিনিই ¯্রষ্টা। থাকেন অন্তরালে।
প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার ঊষালগ্নে রচিত ঔপন্যাসিক হেলিওডোরাসের ঈথিওপিকা ও রোমান ঔপন্যাসিক পেট্্েরানিয়াসের স্যাটাইরিকন উপন্যাস দুটি স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস সাম্প্রতিক হলেও উপন্যাস সাহিত্যের শেকড় কত গভীরে! অবশ্য, উপন্যাসের আধুনিকরূপ আমরা প্রথম দেখতে পাই মিগাল ডে সার্ভান্টেসের ডন কুইক্সোটে (১৬০৫)। উপন্যাসটিতে মনোজগতের গভীরতা, সামাজিক সমালোচনা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রসবোধের প্রতিফলন ঘটেছে। মহাকাব্য ও নাটকের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে উপন্যাসের মধ্যদিয়ে ব্যক্তিচরিত্র, ব্যক্তিমানস ও তাদের অন্তর্জগতের চিত্রায়ন শুরু হয় ।
উপন্যাসের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে স্থান-কাল-পাত্রের ঐক্য অনুসরণ করতে দেখা যায়। সঙ্গত কারণে, সমসাময়িক সমাজের দর্পণ হিসেবে প্রচলিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক প্রভাব ও অস্তিত্বের লড়াই উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস্তববাদের উন্মেষ ঘটে। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স, লিও টলস্টয় ও গুস্টেইভ ফ্লৌবার্ট চরম বাস্তবতার সম্মুখীন হন। সামাজিক ও মনোজগতের বৈচিত্রময় প্রতিফলন ঘটে ডিকেন্সের অলিভার টুইস্ট উপন্যাসে। মানসপটে ভেসে ওঠে দারিদ্রপীড়িত ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডের প্রতিচ্ছবি। টলস্টয়ের অ্যানা কারেনিনা উপন্যাসে দেখা যায়, তদানীন্তন রাশিয়ায় প্রেম-ভালোবাসা, নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক আশা-আকাক্সক্ষার জটিলতা কীভাবে বিভাজন সৃষ্টি করছে।
ইউরোপের বাইরেও তখন গণমানসের কণ্ঠ ও মতামত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটে। জাপানে নাৎসুমি সোসেকির মতো প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকেরাও উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে আধুনিকায়ন ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে ব্যবহার করতে থাকেন। আমেরিকায় মার্ক টোয়েনের মতো প্রভাবশালী ঔপন্যাসিকগণ দাসপ্রথা, বর্ণবাদ, স্বাধীনতা ও সামাজিক বিবেক সম্পর্কিত বিষয়সমূহ উপন্যাসের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেন।
বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উপন্যাসের মৌলিক পরিবর্তন শুরু হয়। সনাতনী বর্ণনা প্রথার পরিবর্তে টুকরো টুকরো মানবমনের স্মৃতির সমাহার ঘটাতে থাকেন। এই ধারায় জেমস জইসের ইউলিসিস (১৯২২) বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। অপরদিকে, ভার্জিনিয়া উলফের টু দ্য লাইটহাউস (১৯২৭) উপন্যাসটিতে সময় ও স্মৃতির প্রতি গুরুত্বপ্রদানে অনীহা পরিলক্ষিত হয়।
আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ অনিবার্যভাবে শিল্পবিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছেন। ফ্রাঞ্জ কাফকার দ্য মেটামরফোসিস (১৯১৫) ও মার্সেল প্রুস্টের ইন সার্চ অব লস্ট টাইম (১৯১৩-১৯২৭) উপন্যাসে এসমস্ত বাহ্যিক উদ্বিগ্নতা ও দ্বন্দ্বের প্রতিফলন ঘটেছে। ক্রমবর্ধমান খ-িত বিশ্বের অর্থ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে।
বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বসাহিত্যে উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের শক্তিশালী অভ্যুদয় ঘটেছে। এ সময়ের উপন্যাসে উপনিবেশবাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, স্থানান্তরিত আবাসন ও পরিবর্তীত পরিচিতির বিষয়গুলি প্রাধান্য পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ চিনুয়া আবের থিংজ ফল আপার্ট, গ্র্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কুয়িজের ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচুড ও সালমান রুশদির মিডনাইট’স চিলড্রেন প্রণিধানযোগ্য। এগুলির মধ্যদিয়ে স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে বৈশ্বিক উদ্বেগ এবং ইউরোপীয় চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত উপন্যাস পরিলক্ষিত হয়।
বর্তমান বিশ্বসাহিতের উপন্যাসে বিভিন্ন ভাষায় উচ্চকিত কণ্ঠ ও বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করা হয়। এ প্রসঙ্গে চিমান্ডা এঙ্গোজি আডিচির হাফ অব আ ইয়োলৌ সান, হারুকি মুরাকামির কাফকা অন দ্য শোর এবং অরুন্ধতি রায়ের দ্য গড অব স্মল থিংজ উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত উপন্যাসে হাইব্রিড কালচার, মাইগ্রেশন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্বব্যাপী মানুষের সাথে উপন্যাসের মাধ্যমে হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপিত হয়।
ঔপন্যাসিকগণ বলার পাশাপাশি মন্তব্য করেন ও বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনীকে বিকশিত করেন যেন তা পাঠককে আনন্দ দান করতে পারে, উত্তেজিত করতে পারে এবং আলোকিত করতে পারে। জর্জ অরওয়েল ও মার্গারেট অ্যাটউডের মতো লেখকগণ রাজনৈতিক সমালোচনা করার জন্য উপন্যাসকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অপরদিকে, মার্সেল প্রাউস্ট ও টনি মরিসন উপন্যাসের মধ্যে মানবিক আবেগ ও মানবমনের স্মৃতির গভীরতা অন্বেষণ করেছেন।
ঔপন্যাসিকগণ কেবল আকর্ষণীয় কাহিনী ও চরিত্রই নির্মাণ করেন না, সমসাময়িক দার্শনিক, সংস্কৃতিক ও নৈতিক জিজ্ঞাসাও উপস্থাপন করে থাকেন। কল্পনার ধারক ও বাহক হিসেবে বাস্তবতার বিপরীতে কল্পনাশ্রয়ী সমাধানের অবতারণা করেন। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করেন। প্রয়োজনে পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেন।
ডিজিটাল মিডিয়ার যুগেও উপন্যাস শক্তিশালী ও গতিশীল মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। নিজস্ব গ-ি পেরিয়ে চলচ্চিত্র, শিল্পকলা ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও ঈর্ষণীয় ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে ঔপন্যাসিকগণ বৈশ্বিক বিষয় যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত বিচ্ছিন্নতা ও সাংস্কৃতিক মেরুকরণ বিষয়ে উপন্যাস লিখছেন। বিষয়বস্তু যাই হোক, সব ধরনের উপন্যাসেই মানবমনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা প্রচ্ছন্ন থাকে। মানবিক হওয়ার বিশ্বস্ত প্রচেষ্টা থাকে।
নাতিদীর্ঘ পরিসরে বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস সম্পর্কে প্রথম দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী ১১টি অধ্যায়ে উপন্যাস জগতের ১১ জন দিকপাল ও তাঁদের উপন্যাস সম্পর্কে প্রচুর তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। এসমস্ত আলোচনা থেকে আমি মনে করি, সময়োপযোগী ও সুলিখিত গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক পাঠকবৃন্দের কৌতুহল নিবৃত্ত করতে সহায়তা করবে। সেই সাথে, তাদেরকে উপন্যাস জগতে বিচরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। উন্নত কাগজ, মজবুত বাঁধাই, ঝকঝকে মুদ্রণ ও দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ গ্রন্থটির মানসম্মত প্রকাশনায় উত্তরণ ঘটিয়েছে। উপন্যাস পাঠে আগ্রহীদের সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই। সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যেও রেফারেন্স বই হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।
স্কুল অব লিবারাল আর্টস অ্যান্ড সোসাল সাইন্সেস
রাজশাহী সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি (আরএসটিইউ)
প্রাক্তন প্রফেসর ও ফোকলোর বিভাগীয় প্রধান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়






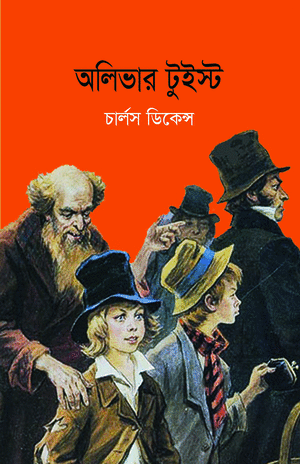




.jpg)


0 মন্তব্যসমূহ